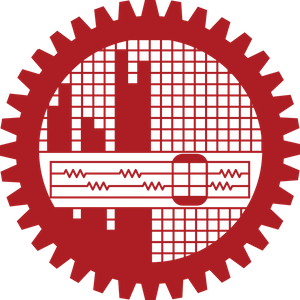
১/ সিনথিয়া কবীর আপুকে দিয়ে শুরু করছি, আপনি বুয়েট থেকে পাশ করার পর পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে আছেন বর্তমানে। আপনার যাত্রাপথ সম্পর্কে কিছু বলুন-
সিনথিয়াঃ আমি বুয়েট সিএসই-২০০৯ ব্যাচ, পাশ করার পর বাংলাদেশে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছি। এরপর আমি ২০১৭ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ইউটাহ থেকে পিএইচডি শুরু করি। আমার রিসার্চ ফোকাস হলো HCI (Human-Computer Interaction).
২/ রুমি আপু, আপনি যদি আপনার সম্পর্কে বলতেন-
রুমিঃ আমি চুয়েট সিএসই-২০০৯ ব্যাচ। ২০১৪ তে গ্র্যাজুয়েশনের পর আমি ঢাকায় ইউআইটিএস আর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে কাজ করি। তারপর আমি ২০১৮ তে ইউনিভার্সিটি অফ আইওয়া তে ডক্টরেট শুরু করি। আমার রিসার্চ ফোকাস শুরুতে ছিল এইচসিআই, বর্তমানে প্যারালাল কম্পিউটিং নিয়ে কাজ করছি।
৩/ নুজহাত আপু, আপনিও যদি আপনার সম্পর্কে শেয়ার করতেন-
নুজহাতঃ আমি চুয়েট সিএসই-২০০৯ ব্যাচ। গ্র্যাজুয়েশনের পর প্রথম জব ছিল রবি আজিয়াটাতে, সেন্ট্রাল অপারেশনে। এরপর ব্র্যাকে লেকচারার হিসেবে জয়েন করি। ২০১৮তে আমি আসি পোল্যান্ডের ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে, এখানে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের উপর মাস্টার্স সম্পন্ন করি। ২০২০ এ মাস্টার্স শেষ হওয়ার আগে থেকেই আমি আমার ইউনিভার্সিটির পার্টনার কোম্পানি স্মার্টলাইফ রোবটিকসে জুনিয়র রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছি।
৪/ আপনাদের তিনজনের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে সংক্ষেপে যদি কিছু বলতেন-
সিনথিয়াঃ আমার বুয়েটে আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের থিসিস ছিল নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির ওপর। কিন্তু এরপর মনে হচ্ছিলো, আমি টপিকটা ঠিক উপভোগ করছি না, মানুষের ওপর সরাসরি ইম্প্যাক্ট পরিবর্তনের ব্যাপারটা লক্ষ করছিলাম না। এরপর ধীরে ধীরে আমি সিদ্ধান্ত নিই, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টার্যাকশন নিয়ে ভবিষ্যত রিসার্চের কাজ করব। বেশ কিছু জায়গায় উচ্চশিক্ষার আবেদন করলেও বেছে নিই ইউনিভার্সিটি অফ ইউটাহকে, কারণ বর্তমান যেই প্রফেসরের সাথে আমি কাজ করছি, তার রিসার্চ এরিয়া অর্থাৎ মানুষের পার্সোনাল ডেটা নিয়ে কাজ করা, এসব ডেটা কিভাবে আমরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারি- এই বিষয়গুলো আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।
বর্তমানে মূলত হেলথ রিলেটেড দুটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি- ১) প্রোস্টেট ক্যান্সার পেশেন্টের বিহেভারিয়াল চেঞ্জ নিয়ে, মানুষ কিভাবে এই চেঞ্জগুলো এডাপ্ট করতে পারে সেটার সাপোর্ট নিয়ে, ২) স্পাইনাল কর্ড পেশেন্টদের জন্য স্মার্ট হসপিটাল- অটোমেশনের মাধ্যমে কিভাবে নিজেদের চিকিৎসায় ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দেওয়া যায়।
রুমিঃ গ্র্যাজুয়েশনের সময় আমার শুরুতে খুব একটা আইডিয়া ছিল না ভবিষ্যৎ রিসার্চ নিয়ে, থিসিস টপিক সংক্রান্ত প্রফেসরদের মেইল করেছিলাম। তারপর ইউনিভার্সিটি অফ আইওয়াতে এইচসিআই নিয়ে একটা হেলথ প্রজেক্টে কাজের সুযোগ পাই। প্রজেক্টটা ছিল অন্ধ ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে এক্সারসাইজের সুযোগ বৃদ্ধি নিয়ে, একটা স্মার্টফোন এ্যাপের মাধ্যমে জগিং ট্র্যাকের ভিজুয়ালাইজেশন করা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া।
পরবর্তী প্রজেক্টের টপিক ছিল, আইওটি ডিভাইসের জন্য কনভোল্যুশনাল নিউরাল নেটওয়ার্কের প্যারামিটারগুলো অপ্টিমাইজ করা, মেমোরি ও এ্যাকুরেসির ট্রেড-অফ নিয়ে কাজ করা। বর্তমানে কাজ করছি তুলনামূলক নতুন টপিক “গ্রাফ নিউরাল নেটওয়ার্ক” নিয়ে, গ্রাফের পরিবর্তনশীল নোড, ফিচারকে নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিভাবে আইওটি ডিভাইসগুলোর জন্য উপযোগী করা যায়, সেটা নিয়ে।
নুজহাতঃ আমার ব্যাচেলর্সের থিসিস ছিল ইমেজ প্রসেসিং নিয়ে, যেটা মূলত রোবোটিক্সেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ওয়ারশ তে আসার পর মেশিন লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং সহ কিছু কোর্স করার সময় আমার মধ্যে রোবটিক্স নিয়ে আগ্রহ বাড়ে, তবে মাস্টার্সের থিসিস ছিল ডেটা সায়েন্সে- ইনফরমেশন ফিউশন মডেলিংএ, টাইম সিরিজ এনালাইসিস নিয়ে।
তবে রোবটিক্স নিয়ে গভীরে কাজ করার আগ্রহ ও সুযোগ দুটোই বেড়েছে স্মার্ট লাইফে জয়েন করার পর। বর্তমানে যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি তা হলো; কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট অফ চাইল্ড, যেটা অনেকটা এইচসিআই এর কাছাকাছি টপিক। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারেক্টিভ বট তৈরি করা, যেটা মূলত শিশুদের লার্নিং, স্পিকিং ও সোশ্যাল এক্টিভিটি উন্নয়নে কাজ করবে। এর সাথেই ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, ভয়েস কমান্ড, স্পিচ রিকগনিশন রিলেটেড আরেকটা প্রজেক্টেও কাজ করেছি। তৃতীয় যে প্রজেক্টে কাজ করছি, তা হল সাইকোমেট্রিক মডেল ডিজাইন। তাই শুধু একজন রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারের কাজের চেয়েও বিশাল পরিসরে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি এখানে।
৫/ শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাগত বা অন্যান্য কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল কখনো?
রুমিঃ আমরা দেশের বাইরে পড়তে আসার আগেই সাধারণত জিআরই/ টোফেলের মত পরীক্ষাগুলো দিয়ে আসি। এখানে আসার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম শুরুতে। “আমার ইউনিভার্সিটি অফ আইওয়াতে বিদেশি নতুন শিক্ষার্থীদের আরোকিছু ভাষাগত পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, যেটার সম্পর্কে আগে থেকে জানা থাকলেও আলাদা করে তেমন প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি।” সেখানে স্কোর কম থাকলে, আরো কিছু কোর্স/ পরীক্ষা যুক্ত করে দেওয়া হয়। আমি আমার স্পিকিং স্কিল নিয়ে মোটামুটি কনফিডেন্ট ছিলাম, কিন্তু প্রাথমিক টেস্টে ফেল এসেছিল। ভাষাগত পরীক্ষার সিস্টেমটা খারাপ নয়, তবে স্কোর কম আসলে যে অতিরিক্ত কোর্স/পরীক্ষাগুলো যুক্ত করা হয়, সেগুলো মূল গ্রেডে প্রভাব ফেলে। কোর্সগুলো থেকে একেবারে নতুন কিছু শেখার সুযোগ যেমন কম, তেমনি অনেক সময়ও নষ্ট হতে পারে। এ ব্যাপারটা আমাকে বেশ অবাক করেছিল, যদিও আমি পাশ করে গিয়েছিলাম। তবে চাইনিজ বা অন্যান্য দেশের বেশকিছু সহপাঠীকেই বেগ পেতে দেখেছি বিষয়গুলো নিয়ে। অনেককে হয়তো মূল ফান্ড হারাতেও হয়েছে, ডিপার্টমেন্টে আলোচনাও হয়েছে ব্যাপারগুলো নিয়ে। তাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা মনে হয়, আমাদের হাতে যেহেতু অপশন থাকেই, ভর্তির আগে ভার্সিটির নিয়ম-কানুনগুলো ভালোভাবে জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে, যেকোনো ধরনের সমস্যাই এড়ানো সম্ভব।
সিনথিয়াঃ আমার অভিজ্ঞতা একটু আলাদা। আমার কাছে যে ভার্সিটির অপশনগুলো ছিল তার মধ্যে Texas A&M University থেকে যে অফার লেটারটা আসে, সেখানে এরকম টেস্টের কথা বলাই ছিল, যেটা আমি চাচ্ছিলাম না। নতুন দেশে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমরা ইতোমধ্যেই অনেক ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাই, এর মধ্যে কোনো অতিরিক্ত চাপ নিতে চাইনি। ইউনিভার্সিটি অফ ইউটাহর ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মকানুন আছে- যেমন টোফেল স্পিকিং এ ২৬ এর নিচে থাকলে আবার ইংলিশ ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সৌভাগ্য বলবো, সেটা আমাকে করতে হয়নি।
ল্যাবমেটদের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে বলবো, আমিই আমার প্রফেসরের প্রথম স্টুডেন্ট ছিলাম, একই বিষয়ের আলোচনা/গল্প করার মত কেউ ছিল না। জিনিসটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারতো, কিন্তু আবারো সৌভাগ্য, আমার প্রফেসর যথেষ্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিলেন। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনতেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করতেন, তবে সবাই যে এমন ভালো প্রফেসর হবেন এমন কিন্তু না। আমার ক্ষেত্রে ভাষা তেমন সমস্যা হয়নি, তবে শুরুর দিকে মানুষেরই অভাব ছিল কথা বলার মতো।
নুজহাতঃ ইউরোপে লোকাল ল্যাংগুয়েজ জানাটাই ওরা প্রাধান্য দেয় সাধারণত, কিন্তু ভার্সিটিতে আমার খুব একটা সমস্যা হয়নি। জার্মানির মতো পোল্যান্ডেও অনেক ডিপার্টমেন্টেই পোলিশ ভাষার কোর্স বাধ্যতামূলক ছিল, তবে আমার ভাগ্য ভালো, আমার ডিপার্টমেন্টে এটা অপশনাল ছিল, জোর করা হয়নি। আমিও সেটা এড়িয়ে গিয়েছি, কঠিন মনে হওয়ায় ভালোমত পোলিশ শিখিনি।
আমরা সাধারণত ব্রিটিশ বা আমেরিকান ইংলিশে অভ্যস্ত। এজন্য শুরুর দিকে শিক্ষকদের পোলিশ ইংরেজি উচ্চারণ/ কথা বলার ধরণ বুঝতে একটু অসুবিধা হতো। বয়স্ক শিক্ষকদের বেলায় সমস্যাটা বেশি হতে পারে। তবে আমার সুপারভাইজরদের সাথে আমার আলোচনায় কোনো সমস্যা হয়নি। আমার মত নতুন বিদেশি শিক্ষার্থীদের শুরুর দিকে নিজে থেকে কথা বলতে/প্রশ্ন করার জড়তা থাকতে পারে। এখানে নিজে থেকে এগিয়ে না আসলে অন্য কেউ সাহায্য করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই শুরুর দিকে ক্লাসে একটু গুটিয়ে থাকলেও, প্রথম সেমিস্টারের পর থেকেই যোগাযোগে মানিয়ে নিয়েছিলাম। নিজে থেকে উদ্যোগী না হলে শিক্ষকরা যদিও এগিয়ে আসবেন না, কিন্তু কোনো কিছু জানতে/শিখতে চাইলে তারা অনেক সাহায্য করেছেন, যেটা কল্পনারও বাইরে।
অফিসের পরিবেশও মূলত ইংরেজিতেই, তাই এখানেও তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।
৬/ পিএইচডির জন্য এপ্লাই, প্রফেসর নির্বাচন কিভাবে করেছিলেন? কোনো কারণে প্রফেসরের সাথে ম্যাচ না হলে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে ট্রানজিশন করে অন্যদিকে যাবার সম্ভাবনা কেমন থাকে?
রুমিঃ সময়মত জিআরই, টোফেল দিয়ে, র্যাংকিং অনুযায়ী ভার্সিটি নির্বাচন ও প্রফেসরদের মেইল করার কাজ শুরু করেছিলাম।
শুরুর দিকে বিদেশি শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই কনফিউজড থাকে, তাছাড়া ন্যাটিভ স্টুডেন্টদের প্রভাবও কিছুটা বেশি থাকে। তাই সবার সাথে মিশে যাওয়া ও কোনো সমস্যা হলে দ্রুত জানানো প্রয়োজন। তবে কোনো ধরনের সমস্যা হলে। অপশন সবসময়ই খোলা থাকে। শুরু থেকেই সবাইকে পজিটিভ থাকতে হবে। রিসার্চের পাশাপাশি কোর্সের রেজাল্টের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত, অন্তত শুরুর দিকে। এতে করে ক্যাম্পাসে একটা ভালো ইম্প্রেশন তৈরি হবে।
প্রফেসর খুবই ভালো, আবার তুমিও তোমার জায়গা থেকে ভালো, তারপরও দুইজনের ঠিক ম্যাচ হচ্ছে না, এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তোমার সম্পর্কে সবার ভালো একটা ভিউ থাকলে, এক প্রফেসরের সাথে কোনো সমস্যা হলে অন্য প্রফেসরদের অপশনগুলো খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। এমনকি অনেক ডিপার্টমেন্টে শুরুর দিকে বিভিন্ন ল্যাবে ঘুরে ঘুরে কাজ করার সুযোগ থাকে, এক বছর পর পছন্দমত প্রফেসরের সাথে কাজ করতে পারবে। তাই আমার উপদেশ থাকবে, শুরু থেকেই খেয়াল রাখতে হবে, সবকিছু তোমার পছন্দমত হচ্ছে কিনা, কোনো ঝামেলা হলে, সেগুলো নোটডাউন করো, অন্যান্য রিসার্চ পথগুলোর কথাও ভেবে দেখতে হবে, দেরি হবার আগেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর কোনো সমস্যা না হলে তো কোনো কথাই নেই।
সিনথিয়াঃ আমরা আমাদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করছি, তার মানে কিন্তু এই না- যে কাউকে নিরুৎসাহিত করছি দেশের বাইরে পড়তে আসতে। আবার আমরা যারা অনেকেই দেশে লেখাপড়া শেষ করে বাইরে পাড়ি জমাই, হয়তো ভাবতে পারি আমাদের জন্য সামনে নির্ঝঞ্ঝাট ভবিষ্যত- ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম না। এজন্য কি কি সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে- এ সম্পর্কে ধারণা থাকলে, যেকোনো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়।
আবেদন প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু করি- জিআরই, টোফেল দেওয়া, প্রফেসরদের নক করার কাজ আমরা সবাই করি। কেউ কেউ রিপ্লাই দেন, তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় আমরা এপ্লাই করি। এরপর যেখান থেকে অফার আসে, সেগুলোর মধ্যে উচ্চ র্যাংকিং এর ভার্সিটিতেই সাধারণত যাওয়ার চিন্তা করি- যেটা সবসময় ভালো নাও হতে পারে। সেরা ভার্সিটিতেও হয়তো অসহযোগী, বাজে প্রফেসর থাকতে পারেন।
সাধারণত যেখান থেকে অফার আসে, সবার সাথেই এডমিশনের আগে বা পরে অন্তত স্কাইপে কল হয়, সেখানে যেকোনো ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। প্রশ্ন নিয়ে আমরা সাধারণত প্রস্তুতি নিই না, আমি আমার সব প্রফেসরদের প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের ল্যাব কালচার কীরকম। আমি আগেই বলেছি, আমার বর্তমান প্রফেসরের আমি প্রথম স্টুডেন্ট, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, “আমি তোমাকে প্রথমে শিখাবো, যখন আমার মনে হবে তুমি একাই চালিয়ে নিতে পারবে, তখন একা ছেড়ে দেবো।” তার কথাটা আমার ভাল লেগেছিল। তবে সত্যি কথা বলতে, বিদেশে নতুন গিয়ে কোনো প্রফেসরের সাথে কাজ করাটা অনেকটা জুয়ার মতো, খাপে খাপ মিলে যেতেও পারে, নাও পারে। আমার সাথে ভালো মিলেছিল বলেই যে সবার সাথে মিলবে, এমনটা কিন্তু না, আমি কয়েকজনের কথা জানি, যাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছিল এবং দুয়েকজন পিএইচডি ড্রপ আউটও করেছিল মানসিক ও কাজের চাপের কারণে। তাহলে সমাধান কি?
শুরু থেকেই সাবধান হতে হবে। ডেডলাইনের আগে দিনরাত কাজ আমরা সবাই করি, কিন্তু প্রফেসর যদি নিয়মিত ১৮ ঘন্টা কাজের নির্দেশ দিয়ে দেন, তাহলে তোমার টেকার সম্ভাবনা কম, অন্য অপশনের খোঁজ করতে হবে। এপ্লাই করা বা ভার্সিটি চয়েস ফাইনাল করার আগে ওখানকার পরিচিতদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিতে হবে- ডিপার্ট্মেন্ট, ল্যাব কালচার কেমন, প্রফেসর কেমন। আমাদের ভার্সিটিতে শুরুর দিকে একটা কোর্সই আছে- “How To Survive Your PhD”, সেখানে প্রফেসররাই বলে থাকেন যে, “অনেকেই ২/৩ বছর কষ্ট করে কাজ করার পর এসে বলে, আমি পারছি না, ড্রপ করতে চাই। এটা কোরোনা,তাহলে ফান্ডিং ও সময়ের অপচয়। প্রথম সেমিস্টার থেকেই যেকোনো সমস্যা মনে হলেই ডিপার্ট্মেন্ট চেয়ার/ অন্য কারো সাথে কথা বলো, সমস্যার কথা জানাও, যাতে আমরা বুঝতে পারি।” আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যার ব্যাপারগুলো কেউ জানায় না।
৭/ সাধারণত ইউএসএই সবার প্রথম পছন্দ থাকে। নুজহাত আপু, আপনি কিভাবে ঠিক করলেন যে ইউরোপেই পড়তে যাবেন? ইউরোপের ভর্তি/প্রস্তুতি পদ্ধতি কতটুকু আলাদা?
নুজহাতঃ আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার পরে ইউরোপে সাধারণত জার্মানি বা ফিনল্যান্ড মানুষ পছন্দ করে। আমি ইউরোপে এসেছি মূলত পারিবারিক কারণে, আলাদা অপশন ছিল না। প্রথম দিকে একটু আফসোস হতো বেটার কোথাও পড়তে না পারার কারণে, কিন্তু যেখানে আছি, সেখানেই যদি খুব ভালো করছি করতে পারি, তাহলে সেই আফসোসটা আর থাকেনা- আমার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে।
IELTS/TOEFL স্কোর দরকার হয় এখানকার ভার্সিটিগুলোর জন্য, রিকোয়ারমেন্ট ভার্সিটি অনুযায়ী আলাদা হয়, তবে ৬/৬.৫ ন্যূনতম হয়ে থাকে। সাথে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আর দেশভিত্তিক ভাষা-দক্ষতার পরীক্ষা লাগে, যেটা আবার পোল্যান্ডে ছিল না, তাই ভাষা-সংক্রান্ত কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি। মাস্টার্সের জন্য এর বাইরে আর কিছু দরকার হয়নি। সাধারণত টিউশন ফি ফ্রি-এর ব্যবস্থা পাওয়া যায়, আর লিভিং আর ফিনান্সিয়াল এক্সপেন্সের জন্য দেশভিত্তিক এপ্লিকেশনের মাধ্যমে যাচাই করে সেন্ট্রালি সহায়তা করা হয়।
৮/ নুজহাত আপু, পোল্যান্ডে আপনি যা যা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, সেগুলো বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানে কাজে লাগানোর সুযোগ কেমন?
নুজহাতঃ মেশিন লার্নিং বলো বা রোবটিক্স বলো, এগুলো সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে এখনো পুরোপুরি উন্নত সেক্টর হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে বা অপশনের কোনো অভাব নেই- ইচ্ছা থাকলেই কাজে লেগে পড়া সম্ভব। যেমন এখানে আমি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিয়ে কাজ করেছি, পোল্যান্ডে নিজেদের ভাষায় এনএলপির যে ভাণ্ডার, তা কিন্তু খুবই উন্নত ও স্ট্রাকচার্ড। সেক্ষেত্রে আমরা যথাযথ সাপোর্ট পেলে বাংলা ভাষার এনএলপি বা স্পিচ রিকগনিশনের কাজগুলো এগিয়ে নিতে পারি। এমনকি পোল্যান্ডের এখানে যেমনটা করা হয়, বই খাতা ছাড়াই রোবটিক্সের সাহায্য নিয়ে ইন্টারেক্টিভ উপায়ে প্রি স্কুল লেভেলে ছোট বাচ্চাদের বর্ণমালা শিক্ষার হাতেখড়ি দেওয়া হয়- এরকম ছোট ছোট উদ্যোগগুলো বাংলাদেশেও নেওয়া যেতে পারে।
৯/ পিএইচডি লাইফে আপনার কোনো উদ্ভট/ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করবেন?
সিনথিয়াঃ প্রফেসরের ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভাগ্য বেশ ভালো, তবে এছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভট পরিস্থিতি দেখতে হয়েছে। যেমন, বিদেশে এখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটির কথা বলি। আমি যখন পিএইচডি করার উদ্দেশ্যে প্রথম এখানে আসি, আমি অবিবাহিত ছিলাম। আমার ফেসবুক প্রোফাইলে আমার সাথে ছোট বাচ্চার (আমার বোনের ছেলে) বেশকিছু ছবি ছিল। এখানে আসার পর আশেপাশের অনেকেই মনে মনে ধরে নেয়, আমি বুঝি আমার ছোট সন্তানকে দেশে একা রেখে পিএইচডি করতে চলে এসেছি (হাসি)।
আরেকটা বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হলো- আমরা বাংলাদেশে একজন আরেকজনের সম্পর্কে না জেনেই জাজ করতে বেশি অভ্যস্ত। যখন ইমিগ্রেশনের পর নতুন দেশে আসি, তখন মনে হতে পারে, এখন বোধহয় কেউ আমাকে অযথা জাজ করবে না, সবাই যেহেতু লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ভুল। এমনও হয়েছে, কোনো একটা অনুষ্ঠান/ দাওয়াতে গিয়ে বারবার শুনতে হয়েছে আমি বিয়ে কবে করছি, বাবা-মাকে দেখতে দেশে যাওয়ার ব্যাপারটাকে অনেকে ধরে নিয়েছে আমি হয়তো বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি ইত্যাদি (হাসি)। অর্থাৎ প্রবাসেও বাংলাদেশিরা আসলে কমবেশি অযথাই মাথা ঘামিয়ে থাকে।
আরেকটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা হলো, আমরা যখন প্রথম দেশের বাইরে পড়তে আসি, আমাদের একাডেমিক লাইফের বড় পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিগত-পারিবারিক জীবনেও একটা বড় পরিবর্তন আসে, বিশেষ করে আমার মত যারা বাবা-মাকে ছেড়ে একা আসি। এখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটি যদিও অনেক বড়, তারপরও সবসময় সাহায্যের নিশ্চয়তা আমি পাইনি। যদিও সবাই খারাপ নন, অনেকেই অনেক হেল্পফুল ছিলেন। বলছি না যে, আমাকে অনেক কষ্টে শুরুর দিকে দিনযাপন করতে হয়েছে, কিন্তু আমি বলব, তোমরা যারা বিদেশে একা পড়তে আসছো, কখনোই বিলাসী/উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবনযাপনের বা আশেপাশের মানুষদের থেকে অনেক বেশি সাহায্যের আশা নিয়ে এসো না। কারণ আমি এমন মানুষও দেখেছি, যারা প্রফেসর কেন ল্যাপটপ কিনতে সাহায্য করেননি, কিংবা পছন্দের খাবার কেন খুঁজে পায়নি- এসব নিয়েও আফসোস করছে (হাসি)। নতুন একটা পরিবেশে, নতুন দেশে অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, এটাই বরং স্বাভাবিক। তাই আশেপাশে বাংলাদেশি থাকুক বা না থাকুক, তোমার এতোটুকু মানসিক শক্তি থাকতে হবে যে, এটা আমার একার জার্নি, যেভাবেই হোক সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে হবে, আমাকে শক্ত থাকতে হবে। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ নিজ যোগ্যতায় বিভিন্ন দেশে স্বনামধন্য জায়গা থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন, এখনো পড়তে আসছেন নিয়মিত, তারা সবাই এই পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে গেছেন,যাচ্ছেন। তারা পারলে, তুমিও অবশ্যই পারবে।
রুমিঃ আমার এখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটি কমবেশি খুবই হেল্পফুল ছিল। রিসিভ করা, খাওয়া দাওয়া, বাজার-সদাই ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সাহায্য পেয়েছি- এটা ভাগ্যের ব্যাপার, সব কমিউনিটি একরকম না। ভালো খারাপ সবধরনের অভিজ্ঞতাই ছিল, যদিও নতুন পরিবেশের জীবন আর পিএইচডির লেখাপড়া সবকিছু মিলিয়ে বেশ চাপ ছিল। সারাদিন কাজ করে এসে রাতে কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানে যেতে সবসময় কিন্তু মন চাইতো না। আর শেষে বলবো, দেশ থেকে আসার সময়ই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে যে একাডেমিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক লাইফে নতুন অনেক কিছু ফেস করতে হতে পারে, সমস্যায় পড়তে হতে পারে। দেশে হয়তো হেল্পিং হ্যান্ড পাওয়া যেত, এখানে কিন্তু সব কাজ একা নিজেরই করতে হবে। মানুষ যে এদিক-ওদিক বেড়াতে বা আনন্দ করতে যায় না তা কিন্তু না, কিন্তু অবশ্যই সেটা পুরো সপ্তাহের কাজের ক্লান্তি দূর করতে, নিজেকে বা পরিবারকে একটু সময় দিতে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে চিল তো করতে পারবেই, কিন্তু যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি সামলে নেবার মানসিকতাও রাখতে হবে।
১০/ বিশেষ করে, নারী হিসেবে আপনারা কোনো ধরনের অসুবিধা/ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন?
নুজহাতঃ আমার ক্ষেত্রে প্রথমত, আমি নিয়মিত হিজাব পরিধান করি। ইউরোপিয়ান বা পশ্চিমা দেশগুলোর সমাজে যেটা একেবারেই প্রচলিত না। ভার্সিটিতে আমার কখনো খুব একটা সমস্যা হয়নি, দুয়েকটা ঘটনা ছাড়া। এখানে দুয়েকজন প্রফেসরের ধারণা এমন যে, হিজাব পরলে বা হেড কভার করলে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা কমে যায় বা চাকরি পাবার ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। কথাটা কিন্তু পুরোপুরি ভুল না, মাস্টার্সের শেষ বর্ষে চাকরির এপ্লাই করার সময়ই কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম। স্থানীয় সমাজ নিজেদের কালচারের বাইরের কিছু এক্সেপ্ট করতে না চাইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকটাই মাল্টিকালচারে বিশ্বাসী। আমার চাকরির ক্ষেত্র যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরেই, আমি সরাসরি বেশি সমস্যা ফেস করিনি এখনো।
আরেকটা জিনিস বলার মতো, এখানকার বিদেশি স্টুডেন্টদের বড় অংশ ইন্ডিয়ান, টার্কিশ বা মিডল ইস্টের, সেক্ষেত্রে পুরনো স্টুডেন্টদের আগে থেকে কোনো খারাপ রেপুটেশন বা রেকর্ড থেকে থাকলে সেটা নতুন স্টুডেন্টসহ সবার মধ্যেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এইদিক থেকেও আমি অনেকটাই ভাগ্যবান, এরকম অভিজ্ঞতা ফেস করতে হয়নি।
১১/ প্রফেসররা পিএইচডি স্টুডেন্ট চয়েস করার ক্ষেত্রে কি কি দেখে থাকেন?
সিনথিয়াঃ এটা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন আমার ক্ষেত্রে, আমার প্রফেসরের যোগদানের প্রথম দিকে, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারেকশন, রিসার্চ ফিল্ড হিসেবে ততটা পপুলার ছিল না। এই ফিল্ডে কাজ করতে আসলে প্রচুর সংখ্যক মানুষের দরকার পড়ে, প্রচুর ডেটা কালেক্ট করতে হয় ম্যানুয়ালি। আমার প্রফেসরের এমন মানুষেরই দরকার ছিল যারা এসবে আগ্রহী, তাই আমার সাথে তার মিলে গেছিলো।
দ্বিতীয়ত, এলাকায়, ভার্সিটিতে বা ডিপার্টমেন্টে স্বদেশিদের নেতিবাচক রেকর্ড যেমন তোমার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিতে পারে, তেমনি আগে থেকে পরিচিত বাংলাদেশিদের ভালো ইম্প্রেশন থাকলে, সেটা তোমার সেলেক্টেড হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।
সাধারণত চাইনিজ/কোরিয়ান/ইরানি প্রফেসরদের কাজপাগল ছাত্র পছন্দ, তারা চান দিনরাত ল্যাবে পড়ে থাকবে, কাজ করবে এমন স্টুডেন্ট জোগাড় করতে, সেক্ষেত্রে তারা বেছে বেছে তাদেরই নেন যারা বেশী পরিশ্রম করতে রাজি। এশিয়ান প্রফেসররা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো ফান্ডিং এর ভয় দেখিয়ে কাজে তাগাদা দিতে পারেন। আবার কিছু কিছু প্রফেসরের ক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কোনো স্কিল/দক্ষতা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, যেমন আমার ক্ষেত্রে প্রফেসর চাইতেন তার ছাত্র ধীরে ধীরে শিখুক, সব জানুক। আবার অনেকেই ধরে নেবেন, তুমি আগে থেকেই জানো অনেককিছু, তোমার পাবলিকেশনে নজর দেবেন।
আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো রিকমেন্ডেশন লেটার, সাধারণত এদেশের পরিচিত মুখের প্রফেসর না হলে, বাইরের প্রফেসররা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেন না লেটারটাকে কিভাবে নেওয়া উচিত। তাই আমার উপদেশ হলো, সিজিপিএ ভালো রাখার চেষ্টা কর, GRE/TOEFL এর সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নাও, পাশাপাশি রিকমেন্ডেশন লেটারে ফোকাস দাও, যাতে সেখানে রিসার্চের কথা থাকে। কোর্স রেজাল্টের চেয়ে অবশ্যই রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্সের রিকমেন্ডেশনের দাম বেশী। আর সবসময়ই প্রফেসররা চান তুমি কতটা নেতৃত্ব দিতে পারো বা সবার সাথে কম্যুনিকেট করতে পারো।
রুমিঃ আমিও একমত- প্রতিটা প্রফেসরের মেন্টালিটিই আসলে আলাদা- নির্দিষ্ট করে বলা খুব কঠিন যে তারা আসলে তোমার মধ্যে কী খুঁজছেন। আমার মনে হয়, স্টেটমেন্ট অফ পারপাজ (SoP) লেখাটার গুরুত্ব অনেক, আন্ডারগ্র্যাডে রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে খুবই ভালো, যদিও এটা আমাদের অধিকাংশেরই থাকে না।
অনেকেরই প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই টার্গেট থাকে বাইরে পড়তে যাওয়ার, সেক্ষেত্রে ফ্যাকাল্টি রিসার্চের সুযোগগুলো কাজে লাগানো উচিত। সিজিপিএ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু আমার মনে হয় না একটু নিয়মিত কষ্ট করলে বাংলাদেশে আমাদের সিজি উঠানো খুব একটা কঠিন কিছু না। তাই রেজাল্ট আর স্কিল দুটোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
১২/ ইন্ডাস্ট্রি বা একাডেমিয়া ট্র্যাক দুটোকে কিভাবে দেখেন? আপনাদের ক্যারিয়ার চয়েসের পেছনে কারণ/মোটিভেশন কী ছিল?
সিনথিয়াঃ এখানে ট্যানিউর ট্র্যাক থেকে উপরে ওঠার রাস্তাটা কিন্তু বেশ কষ্ট ও সময়সাপেক্ষ। ব্যক্তিগতভাবে, ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ, বিশেষ করে Research and Development সেক্টরের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। তাই আমি বলব না যে, আমি একাডেমিয়া বেছে নিয়েছি। যদিও আমি শিক্ষকতাও করেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চে শিফট করার ইচ্ছা বেশি।
রুমিঃ আমার কাছে মনে হয়, এখানে বোধহয় ইন্ডাস্ট্রিই বেটার, কারণ ৯-৫টা কাজ করার পর মানসিক শান্তি থাকে যে, আজকের মতো কাজ শেষ হয়েছে- যেখানে তুলনামূলকভাবে একজন ট্যানিউর ট্র্যাকের এসিস্টেন্ট প্রফেসরের কাজের চাপ বিশাল। এই বিষয়টা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আবার একেবারেই উল্টা- গ্র্যাজুয়েশনের পরপরই প্রায় সবাই লেকচারার হিসেবে জয়েন করি, যেখানে আসলে তেমন নতুন কিছুই শেখা হয়না।
আমার ব্যক্তিগত অভিমত, যদি দেশে শুরুতে কয়েক বছর কাজ করে বাইরে শিফট করার ইচ্ছা থাকে- সেক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি চয়েস করাই বেটার- বাইরে যাবার আগে দেশে হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতাও পাওয়া যাবে। যেটা আমার মনে হয় না, প্রাইভেট ভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে জয়েন করার পর খুব একটা শেখা যায়।
১৩/ সিনথিয়া আপু, আপনি তো BWCSE (Bangladeshi Women in Computer Science and Engineering) এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন- আপনার এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন-
সিনথিয়াঃ BWCSE যখন শুরু করি আমি তখন ৩-২ তে ছিলাম। বুয়েটের ২০০০ ও ২০০২ ব্যাচের দুজন এলামনাই- যারা দুজনই এখন ইউএসএতে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি, তারা প্রথম বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য এরকম একটা প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে উদ্যোগ নেন। আপুরা স্যারদের সাথে যোগাযোগ করেন, স্যার আমাকে দায়িত্ব দেন সবকিছু ব্যবস্থা করার। ভলান্টিয়ারি কাজে মানুষের কতটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, তা তো তোমরা জানোই, তাই আমি বলব না শুরুর দিকে আমি খুব বেশি মানুষের সাহায্য পেয়েছি। একা একাই অনেক কিছু করতে হয়েছিল- এমনকি হয়তো পরীক্ষার দিন সকাল বেলা গিয়ে সেশন আয়োজনের রুমবুকের জন্যও এপ্লিকেশন করতে হয়েছিল।
অনেকেই শুরুতে ভলান্টারি সময় দিতে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টোটা, আমি এই ক্লাবকে এগিয়ে নিতে গিয়ে এতো মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি- যোগাযোগ করেছি বিভিন্ন সেশন আয়োজনের জন্য- এটা খুবই উপকারী একটা অভিজ্ঞতা ছিল আমি বলব। শুরুতে হয়তো স্যারদের দেওয়া দায়িত্ব রাখার জন্যই কাজ করতাম- ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি ক্লাবটার সাথে লেগে থেকে, কাজ করে আমারও কত লাভ হয়েছে। এমনকি গ্র্যাজুয়েশন পুলে এপ্লাই করার সময় তোমার SoP তে তুমি যদি উল্লেখ করতে পারো- আমি এরকম একটা ক্লাবের সাথে যুক্ত আছি, বেশকিছু টেকনিকাল-নেটওয়ার্কিং সেশন আয়োজন করেছি, তাহলে সেটা প্রফেসর খুবই ভালোভাবে নেবেন- যে এই স্টুডেন্ট আমার ল্যাবের জন্য ইন্টারেক্টিভ হবে, বাকি সবাইকে লিড দিতে, সাহায্য করতে পারবে।
১৪/ কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে, বর্তমানে আপনাদের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন-
রুমিঃ এটা আসলে আমাদের সবাই জন্যই ইউনিক একটা অভিজ্ঞতা, যদি বেঁচে থাকি সবাই- সারাজীবন মনে রাখার মতো একটা ঘটনা হয়ে থাকবে। আর সবমিলিয়ে মিশ্র অনুভূতি- ক্লাসের কিংবা কাজের ভবিষ্যত পরিস্থিতির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এখন এমনিতেও চাকরির বাজারে সমস্যা চলছেই বিশ্বজুড়ে- জীবন থাকলেই যেহেতু জীবিকার চিন্তা চলে আসে, তাই আমাদের পিএইচডি স্টাডির ওপর কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা- এসব নিয়েও চিন্তিত সবাই। কাজের ক্ষেত্রে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ এর পথকেই বেছে নিয়েছি সবাই- এ নিয়ে আমাদের খুব একটা চিন্তার কারণ নেই। আর কাজ-লেখাপড়ার মধ্যেও আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, ভালোমন্দ খোঁজ রাখার দুশ্চিন্তাটা এসে গেছে- যেটা হয়তো আগে এতো ছিলনা।
সিনথিয়াঃ আমার আসলে এই গ্রীষ্মে দেশে আসার কথা ছিল- স্বাভাবিকভাবেই সব প্ল্যান বাতিল এখন। বাবা-মাকে নিয়ে আসলেই চিন্তিত- কোভিড ১৯ পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক বাংলাদেশে। মার্চের দিকে আমরা ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ মেনে চলা শুরু করি। প্রথম দুয়েক-সপ্তাহ অনেক বাজে কেটেছিল, কাজে মন বসাতে পারছিলাম না- এমনকি প্রফেসরকেও জানিয়ে রেখেছিলাম দুরবস্থার কথা। যদিও আমার কাজ হাসপাতাল ঘিরেই এখন, তারপরও বাসায় থেকে কাজে আসলে খুব একটা সমস্যা হয়না- কিন্তু দুশ্চিন্তা তো লেগেই আছে। কখন দেশে যাবো- এটা ভেবেই কষ্ট লাগে আসলে, যেহেতু আমি পৃথিবীর প্রায় অন্য আরেক প্রান্তে- পরিবার থেকে অনেক দূরে।
১৫/ যারা এখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে লেখাপড়া করছে, বা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস- তাদের জন্য আপনাদের উপদেশ বা সাজেশনগুলো যদি বলতেন-
নুজহাতঃ সিএসই খুবই ভার্সেটাইল একটা কারিকুলাম, এটার অনেক ব্রাঞ্চও আছে। যদি এমন হয় যে, তোমার এলগোরিদম, ডেটা স্ট্রাকচার কিংবা সফটওয়্যারে কোথাও ঘাটতি বা দুর্বলতা আছে, কিন্তু ধরো নেটওয়ার্কিং বা সিকিউরিটি নিয়ে তুমি খুব ভালো জানো, সেক্ষেত্রে কিন্তু জব বা ক্যারিয়ার অপরচুনিটির কোনো অভাব নেই। আবার চাইলে রিসার্চ/ডাটা সায়েন্স ফিল্ডেও আসতে পারো। এখানে থিওরির পাশাপাশি স্কিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তোমাকে কাজ জানতে হবে। নতুন কন্সেপ্ট, থিওরি বা টেকনোলজির সাথে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা থাকা জরুরি। আমি নিজেও কাজ করতে করতেই অনেক কিছু শিখেছি এখানে। আত্মবিশ্বাস, ইন্সট্যান্ট লার্নিং আর চ্যালেঞ্জ নেওয়ার দক্ষতাও খুবই দরকারি। সবাইকে যে অসাধারণ প্রোগ্রামার হতে হবে এমন না, কিন্তু নিজের একটা লার্নিং স্ট্র্যাটেজি দাঁড় করাতে শিখতে হবে।
রুমিঃ শুরু থেকেই আসলে ক্যারিয়ারের চিন্তাভাবনায় যত্নবান হতে হবে, নিজের প্রোফাইল ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে। বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত থাকা, কম্পিটিশনে অংশ নেওয়া- এসবই ভবিষ্যতে অনেক কাজে দিবে। আগে থেকে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বাইরে আসলে কেনো আসতে চাচ্ছ। আর যেকোনো সময়ে মেন্টাল ব্রেকডাউনে যাতে না পড়তে হয় সেজন্য সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে- বন্ধুবান্ধব সবার সাথে শেয়ার করতে পারলে ভালো। আর বিশেষ করে বাংলাদেশি মেয়েদের জন্য বলব- তোমরা আরো বেশি বেশি বাইরে পড়তে আসো- আমার নিজের ক্ষেত্রেই যদি বলি- নিজ ডিপার্টমেন্টে একজন দেশি মেয়ে পেলে হয়তো আরো অনেক কিছু শেয়ার করতে পারতাম যেকোনো প্রয়োজনে।
সিনথিয়াঃ মাস্টার্স বা পিএইচডি, যেটাই করতে আসবে ঠিক করোনা কেন, নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে- যে একটু কষ্টকর জার্নি হবে, কিন্তু তুমি পারবেই। নিজের কাজের প্রতি প্যাশনেট হতে হবে। কমিটমেন্ট আসলেই রাখতে চাও কিনা সেগুলো নিশ্চিত করে তবেই সিদ্ধান্ত নিও। অন্য কোনো কিছু বা চাকরির দায়িত্ব থেকে বাঁচতে পিএইচডি করতে আসার কথা চিন্তাও কোরোনা। আর মানুষের সাথে বেশি বেশি মিশতে হবে। আমার কর্মক্ষেত্রেও মেয়ে সহপাঠী বা দেশি মানুষ পেলে হয়তো অনেক সুবিধা হতো, আমি, রুমি- আমরা নিজেদের ফেসবুক গ্রুপ চ্যাটেই যোগাযোগ রাখতাম- ভালোমন্দ শেয়ার করতাম।
আরেকটা বিষয়ে কেউ আমাদের সচরাচর খেয়াল রাখতে বলে না বা জোর দেয়না- তা হল স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল কিন্তু নিজেকেই হতে হবে। তাই যেটাই করো না কেন- নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।